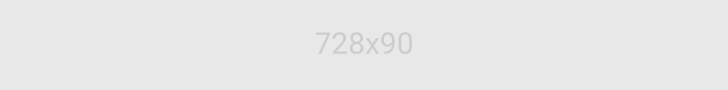বাংলাদেশের নির্বাচন সংকট: আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ চাপের দ্বন্দ্ব
পবিত্র মজুমদার
সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে উত্তেজনা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি জানালেও, বর্তমান সরকারের আচরণ থেকে মনে হচ্ছে তারা নির্বাচনকে বিলম্বিত করতে চাইছে। তবে এই বিলম্ব শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয় নয়। কিছু বড় আন্তর্জাতিক পরাশক্তি, যাদের কৌশলগত স্বার্থ বর্তমান সরকারের সাথে যুক্ত, তারা পরোক্ষভাবে এই দীর্ঘায়িত শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করছে। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি শক্তির প্রভাব নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তৈরি করছে।
বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন নিয়ে আলোচনায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে আসছে প্রথমটি আন্তর্জাতিক চাপ এবং দ্বিতীয়টি অভ্যন্তরীণ চাপ।
আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি : বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক চাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির মাধ্যমে। বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া ও মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগ থাকলেও, যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিতে বাংলাদেশ একটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ দেশ। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া ও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের সমীকরণে বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও রাজনৈতিক পরিবেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তবে, যুক্তরাষ্ট্র কখনোই বাংলাদেশের নির্বাচন ইস্যুতে সরাসরি শক্ত অবস্থান নেয়নি। এর পেছনে রয়েছে ভূরাজনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থ। এই প্রেক্ষাপটে, যুক্তরাষ্ট্র আরাকান আর্মিকে জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে এবং বাংলাদেশকে এ অঞ্চলে একটি কৌশলগত অংশীদার হিসেবে দেখছে।
এই প্রেক্ষাপটে একটি প্রশ্ন সামনে আসে— বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যদি যুক্তরাষ্ট্রের ভূরাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ হতে রাজি হয়, বিশেষ করে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করতে চায়, তবে যুক্তরাষ্ট্রও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার নামে বর্তমান সরকারকে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার সুযোগ দিতে পারে। এ কারণে আমি মনে করি, আগামী ছয় মাস বা এক বছর নয় বরং পাঁচ বছরেও যদি নির্বাচন না হয়, সেটি যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি : ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার খুব সম্প্রতি বলেছেন, বাংলাদেশে নির্বাচনের নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কোনো চাপ নেই। বরং জোটটির মতে, প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সম্পন্নের জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া উচিত। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই অবস্থান বিশেষভাবে অপ্রত্যাশিত নয়, কারণ যুক্তরাষ্ট্রও বিভিন্নভাবে এই বার্তাই দিচ্ছে—সংস্কারের জন্য সরকারকে সময় দেওয়া উচিত। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীত অবস্থান নেবে না, তা সহজেই অনুমান করা যায়। যদিও আমরা দেখেছি, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শাসনামলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে কিছুটা টানাপোড়েন দেখা গিয়েছিল—বিশেষ করে রাশিয়া-ইউক্রেন ইস্যু এবং পারস্পরিক শুল্কনীতি (reciprocal tariff) নিয়ে। তবুও বড় কৌশলগত প্রশ্নে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কখনোই যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি। বর্তমান প্রেক্ষাপটও সে ধারারই প্রতিফলন, যা আবারও প্রমাণ করে যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার যতদিনই সময় নিক না কেন, সংস্কারের নামে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাতে সমর্থন জানাবে এবং পাশে থাকবে।
ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে ঘনিষ্ঠ হলেও সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের কৌশলগত অবস্থানে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা ইঙ্গিত দিয়েছেন, নির্বাচনের মাধ্যমে একটি বৈধ ও নির্বাচিত সরকার গঠিত হলে তবেই তারা দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনা করবেন। ফলে ভারতের পক্ষ থেকে সীমিত পর্যায়ে হলেও একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কিছুটা চাপ সৃষ্টি হতে পারে।
তবে আন্তর্জাতিক চাপ বলতে মূলত বোঝায় যুক্তরাষ্ট্র এবং কিছু ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে। কিন্তু বাস্তবতা হলো—বর্তমান সরকার আন্তর্জাতিক কৌশলগত স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় জোটের সঙ্গে যেভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে, তাতে তাদের কাছ থেকে কোনো বাস্তবধর্মী নির্বাচনী চাপ আসার সম্ভাবনা খুবই কম। বরং স্থিতিশীলতার নামে তারা বর্তমান সরকারকেই সমর্থন দিয়ে যাবে।
অভ্যন্তরীণ চাপ: বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নির্বাচনী দাবির মধ্যে একাধিক মতভেদ এবং অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে, যা দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরও জটিল করছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজস্ব দাবী তুলে ধরছে, যার ফলে নির্বাচনের সময় এবং পদ্ধতি নিয়ে অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে।
জাতীয় নাগরিক কমিটি : এই দল মনে করছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে নির্বাচন আয়োজন সঠিক সময় নয়। তাদের মতে, সরকারের উচিত আরো কিছু সময় অপেক্ষা করা এবং সঠিক সময় নির্বাচনের আয়োজন করা। তাদের দাবি, বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক চাপ ও অস্থিরতা নির্বাচন প্রক্রিয়ার জন্য অনুকূল নয়।
বিএনপি : বিএনপি বরাবরই দ্রুত নির্বাচনের পক্ষে এবং তারা সরকারের কাছে নির্বাচনের একটি রোড ম্যাপ দাবি করছে। তাদের মতে, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন ছাড়া দেশ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। তারা সতর্ক করে দিয়েছে যে, যদি নির্বাচন দেরি হয়, তবে দেশের অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি আরও সংকটে পড়বে। বিএনপি জনগণের দাবী অনুযায়ী দ্রুত নির্বাচন চায় এবং একে দেশের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত জরুরি মনে করে।
জাতীয় পার্টি : জাতীয় পার্টিও দ্রুত নির্বাচনের পক্ষে। তারা নির্বাচনের রোড ম্যাপ চাচ্ছে এবং মনে করছে, নির্বাচন না হলে রাজনৈতিক দলগুলো ও জনগণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যাবে। তাদের দাবি, নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা জরুরি।
ইসলামিক দলগুলো : ইসলামী দলগুলোও এই বছরের মধ্যে নির্বাচন চাচ্ছে, তবে তারা একাধিকবার বলেছে যে, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত।
সরকারের অবস্থান: সরকারের পক্ষ থেকে সংস্কারের কথা বলা হলেও, নির্বাচনের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা করা হয়নি। কখনো বলা হচ্ছে, ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন হবে, আবার কখনো বলা হচ্ছে, আগামী বছরের মাঝামাঝিতে নির্বাচন আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। এমনকি কিছু সময় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, নির্বাচনের আগে কিছু সংস্কারের প্রয়োজন, যা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আরো বিভাজন এবং ধোঁয়াশা তৈরি করেছে।
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট : আমি মনে করি, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন আয়োজনের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে কোনো জোরালো চাপ আসবে না। কারণ বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থান তৈরি করছে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য। এশিয়া এবং ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে একটি সম্ভাব্য মিত্র হিসেবে দেখছে। রোহিঙ্গা সংকট, মিয়ানমার পরিস্থিতি ও চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশকে পাশে পাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্বার্থে পরিণত হয়েছে। ফলে, তারা হয়তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও মানবাধিকার নিয়ে বক্তব্য দিলেও, বাস্তবে তারা বর্তমান সরকারের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার দিকেই বেশি গুরুত্ব দেবে।
অভ্যন্তরীণ চাপ ও সংকট: বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপ বর্তমানে ক্রমেই বাড়ছে। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো—বিএনপি, জাতীয় পার্টি এবং ইসলামিক দলগুলো—তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিরপেক্ষ ও সময়োপযোগী নির্বাচনের দাবি জানিয়ে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। সরকার একদিকে সংস্কারের কথা বললেও, নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট সময়সীমা বা রোডম্যাপ ঘোষণা না করায় রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিভ্রান্তি বাড়ছে। এই অস্পষ্টতা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থাহীনতা তৈরি করছে এবং সাধারণ জনগণের মাঝেও হতাশা বাড়ছে। যদি অভ্যন্তরীণ চাপ অব্যাহত থাকে, তবে সরকারকে দ্রুত সময় মধ্যে নির্বাচনের পথে আসতেই হবে। অন্যথায় এই চাপ উপেক্ষা করলে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পাবে, যা সহিংস আন্দোলন, জনআন্দোলন বা সুশাসনের প্রতি জনমনে অনাস্থার জন্ম দিতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে এই অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশের অর্থনীতি, সামাজিক ভারসাম্য এবং প্রশাসনিক স্থিতিশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অতএব, এই সংকট নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে স্বচ্ছ এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণই হতে পারে সবচেয়ে কার্যকর সমাধান।
শিক্ষার্থী,সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়